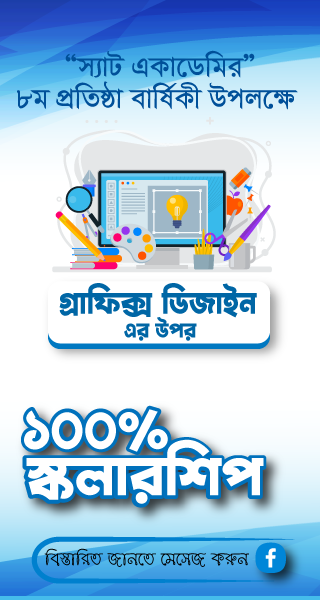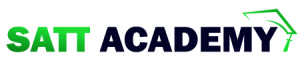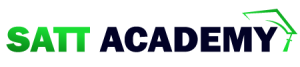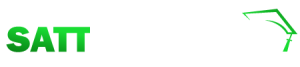চাঁদনি থেকে নয়সিকে দিয়ে একটা শার্ট কিনে নিয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিচক্ষণ বাঙালির জন্য ইয়োরোপিয়ান থার্ড নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র আনাগোনা করত । হাওড়া স্টেশনে সেই থার্ডে উঠতে যেতেই এক ফিরিঙ্গি হেঁকে বলল, “এটা ইয়োরোপিয়ানদের জন্য ।”
আমি গাঁক গাঁক করে বললুম, “ইয়োরোপিয়ান তো কেউ নেই। চল, তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই ।” এক তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, “বাংলা শব্দের অন্ত্যদেশে অনুস্বার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়; ইংরেজি শব্দের প্রাগদেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবি ইংরেজি হয়।” অর্থাৎ পয়লা সিলেবলে অ্যাকসেন্ট দেওয়া খারাপ রান্নায় লঙ্কা ঠেসে দেওয়ার মতো— সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সোজা বাংলায় এরই নাম গাঁক গাঁক করে ইংরেজি বলা। ফিরিঙ্গি তালতলার নেটিভ, কাজেই আমার ইংরেজি শুনে ভারি খুশি হয়ে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল।
কিন্তু এদিকে আমার ভ্রমণের উৎসাহ ক্রমেই চুপসে আসছিল। এতদিন পাসপোর্ট জামাকাপড় যোগাড় করতে
ব্যস্ত ছিলুম, অন্য কিছু ভাববার ফুরসত পাইনি। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে ভাবনা আমার মনে উদয়
হলো সেটা অত্যন্ত কাপুরুষজনোচিত— মনে হলো আমি একা । ফিরিঙ্গিটি লোক ভালো। আমাকে গুম হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, “এত মনমরা হলে কেন? গোয়িং ফার?” দেখলুম, বিলিতি কায়দা জানে। “হোয়ার আর ইউ গোয়িং?” বলল না ।
তা সে যাই হোক, সায়েবের সঙ্গে আলাপচারিতা আরম্ভ হলো। তাতে লাভও হলো। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে প্রকাণ্ড এক চুবড়ি খুলে বলল, তার 'ফিয়াসে' নাকি উৎকৃষ্ট ডিনার তৈরি করে সঙ্গে দিয়েছে এবং তাতে নাকি একটা পুরাদস্তুর পল্টন পোষা যায়। আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম যে আমিও কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি, তবে সে নিতান্ত নেটিভ বস্তু, হয়ত বড্ড বেশি ঝাল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর স্থির হলো, সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে ব্রাদারলি ডিভিশন করে আলাকার্ত ভোজন, যার যা খুশি খাবে।
সায়েব যেমন যেমন তার সব খাবার বের করতে লাগল, আমার চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জমে যেতে লাগল । সেই শিককাবাব, সেই ঢাকাই পরোটা, মুরগি মুসল্লম, আলু-গোস্ত। আমিও তাই নিয়ে এসেছি জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে ।
এবার সায়েবের চক্ষুস্থির হওয়ার পালা। ফিরিস্তি মিলিয়ে একই মাল বেরোতে লাগল। এমনকি শিককাবাবের জায়গায় শামিকাবাব নয়, আলু-গোস্তের বদলে কপি-গোস্ত পর্যন্ত নয়। আমি বললুম, “ব্রাদার, আমার ফিয়াসে নেই, এসব জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে কেনা।”
একদম হুবহু একই স্বাদ । সায়েব খায় আর আনমনে বাইরের দিকে তাকায় । আমারও আবছা আবছা মনে পড়ল, যখন সওদা করছিলুম তখন যেন এক গাব্দাগোব্দা ফিরিঙ্গি মেমকে হোটেলে যা পাওয়া যায় তাই কিনতে দেখেছি। ফিরিঙ্গিকে বলতে যাচ্ছিলুম তার ফিয়াসের একটা বর্ণনা দিতে, কিন্তু থেমে গেলুম।
ভোর কোথায় হলো মনে নেই। জুন মাসের গরম পশ্চিমে গৌরচন্দ্রিকা করে নামে না। সাতটা বাজতে না বাজতেই চড়চড় করে টেরচা হয়ে গাড়িতে ঢোকে আর বাকি দিনটা কী রকম করে কাটবে তার আভাস তখনই দিয়ে দেয় ৷ গাড়ি যেন কালোয়াত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, কোনো গতিকে রোদ্দুরের তবলচিকে হার মানিয়ে যেন কোথাও গিয়ে ঠাণ্ডায় জিরোবে। আর রোদ্দুরও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে ততোধিক ঊর্ধ্বশ্বাসে। সে পাল্লায় প্যাসেঞ্জারদের প্রাণ যায় । গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে। দাড়ি লম্বা হয়েছে, টিকি খাটো হয়েছে, নাদুসনুদুস লালাজিদের মিষ্টি মিষ্টি ‘আইয়ে বৈঠিয়ে' আর শোনা যায় না। এখন ছ-ফুট লম্বা পাঠানদের ‘দাগা, দাগা, দিলতা, রাওড়া,' পাঞ্জাবিদের ‘তুবি, অসি', আর শিখ সর্দারজিদের জালবন্ধ দাড়ির হরেক রকম বাহার ।
সামনের বুড়ো সর্দারজিই প্রথম আলাপ আরম্ভ করলেন। 'গোয়িঙ্গ ফার?' নয়, সোজাসুজি ‘কহাঁ জাইয়েগা?' আমি ডবল তসলিম করে সবিনয় উত্তর দিলুম— ভদ্রলোক ঠাকুরদার বয়সী আর জবরজঙ্গ দাড়ি-গোঁফের ভিতর অতি মিষ্ট মোলায়েম হাসি। জিজ্ঞাসা করলেন, পেশাওয়ারে কাউকে চিনি? না হোটেলে উঠব। বললুম ‘বন্ধুর বন্ধু স্টেশনে আসবেন, তবে তাঁকে কখনো দেখিনি, তিনি যে আমাকে কী করে চিনবেন সে সম্বন্ধে ঈষৎ উদ্বেগ আছে।' সর্দারজি হেসে বললেন, “কিছু ভয় নেই, পেশাওয়ার স্টেশনে এক গাড়ি বাঙালি নামে না, আপনি দু-মিনিট সবুর
করলেই তিনি আপনাকে ঠিক খুঁজে নেবেন।”
আমি সাহস পেয়ে বললুম, “তা তো বটেই, তবে কিনা শার্ট পরে এসেছি—” সর্দারজি এবার অট্টহাস করে বললেন, “শার্টে যে এক ফুট জায়গা ঢাকা পড়ে তাই দিয়ে মানুষ মানুষকে চেনে নাকি?” আমি আমতা আমতা করে বললুম, “তা নয়, তবে কিনা ধুতি-পাঞ্জাবি পরলে হয়ত ভালো হতো।”
সর্দারজিকে হারাবার উপায় নেই। বললেন, “এও তো তাজ্জবকি বাত- পাঞ্জাবি পরলে বাঙালিকে চেনা যায়?”
আমি আর এগলুম না। বাঙালি ‘পাঞ্জাবি’ ও পাঞ্জাবি কুর্তায় কী তফাত সে সম্বন্ধে সর্দারজিকে কিছু বলতে গেলে তিনি হয়ত আমাকে আরও বোকা বানিয়ে দেবেন। তার চেয়ে বরঞ্চ উনিই কথা বলুন, আমি শুনে যাই । জিজ্ঞাসা করলুম, “সর্দারজি শিলওয়ার বানাতে ক-গজ কাপড় লাগে ?”
বললেন, “দিল্লিতে সাড়ে তিন, জলন্ধরে সাড়ে চার, লাহোরে সাড়ে পাঁচ, লালমুসায় সাড়ে ছয়, রাওলপিন্ডিতে সাড়ে সাত, তারপর পেশাওয়ার এক লক্ষে সাড়ে দশ, খাস পাঠানমুল্লুক কোহাট খাইবারে পুরো থান।”
‘বিশ গজ!’
“হ্যাঁ, তাও আবার খাকি শার্টিং দিয়ে বানানো । ”
আমি বললুম, “এ রকম এক বস্তা কাপড় গায়ে জড়িয়ে চলাফেরা করে কী করে? মারপিট, খুন-রাহাজানির কথা বাদ দিন।”
সর্দারজি বললেন, “আপনি বুঝি কখনো বায়স্কোপ যান না? আমি এই বুড়োবয়সেও মাঝে মাঝে যাই । না গেলে ছেলে-ছোকরাদের মতিগতি বোঝাবার উপায় নেই— আমার আবার একপাল নাতি-নাতনি। এই সেদিন দেখলুম, দুশো বছরের পুরোনো গল্পে এক মেমসায়েব ফ্রকের পর ফ্রক পরেই যাচ্ছেন, পরেই যাচ্ছেন— মনে নেই, দশখানা না বারোখানা। তাতে নিদেনপক্ষে চল্লিশগজ কাপড় লাগার কথা। সেই পরে যদি মেমরা নেচেকুঁদে থাকতে পারেন, তবে মদ্দা পাঠান বিশগজি শিলওয়ার পরে মারপিট করতে পারবে না কেন?” আমি খানিকটা ভেবে বললুম, “হক কথা; তবে কিনা বাজে খরচ।”
ইতোমধ্যে গল্পের ভিতর দিয়ে খবর পেয়ে গিয়েছি যে পাঠানমুল্লুকের প্রবাদ, “দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের।” শুনে গর্ব অনুভব করেছি বটে যে বন্দুকধারী পাঠান কামানধারী ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিন্তু বিন্দুমাত্র আরাম বোধ করিনি। গাড়ি পেশাওয়ার পৌঁছবে রাত নয়টায়। তখন যে কার রাজত্বে গিয়ে পৌছব তাই মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি; এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল ।
২
প্ল্যাটফরমে বেশি ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ করলুম যে ছ-ফুটি পাঠানদের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের বাঙালিত্ব জাহির করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এসে উত্তম উর্দুতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে এক হাত এগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর দুহাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ- পরম উৎসাহে, গরম সংবর্ধনায়। সে চাপে আমার হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর দুই থাবার ভিতর তখন লুকোচুরি খেলছে।
খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না, জানেন না, আমি বাঙালি তিনি পাঠান। তবে যে এত সংবর্ধনা করছেন তার মানে কী? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?
আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক । অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মতো আনন্দ পাঠান অন্য কোনো জিনিসে পায় না আর সে অতিথি যদি বিদেশি হয় তা হলে তো আর কথাই নেই ।
৩
আরবি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে “ইয়োম উস সফর, নিস্ফ উস্ সফ্র” অর্থাৎ কিনা যাত্রার দিনই অর্ধেক ভ্রমণ। পূর্ব বাংলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেখানে বলা হয়, ‘উঠোন সমুদ্র পেরলেই আধেক মুশকিল আসান।' আহমদ আলীর উঠোন পেরোতে গিয়ে আমার পাক্কা সাতদিন কেটে গেল। আটদিনের দিন সকালবেলা আহমদ আলী স্বয়ং আমাকে একখানা বাসে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে তাকে আমার জান-মাল বাঁচাবার জন্য বিস্তর দিব্যদিলাশা দিয়ে বিদায় নিলেন। হাওড়া স্টেশনে মনে হয়েছিল ‘আমি একা’, এখন মনে হলো ‘আমি ভয়ংকর একা’। ‘ভয়ংকর একা' এই অর্থে যে নো ম্যানস ল্যান্ডই বলুন আর খাস আফগানিস্তানই বলুন, এসব জায়গায় মানুষ আপন আপন প্রাণ নিয়েই ব্যস্ত ।
সাধারণ লোকের বিবেকবুদ্ধি এসব দেশে এরকম কথাই কয়। তবু আফগানিস্তান স্বাধীন সভ্য দেশ; আর পাঁচটা দেশ যখন খুন-খারাবির প্রতি এত বেমালুম উদাসীন নয় তখন তাঁদেরও তো কিছু একটা করবার আছে এই ভেবে দু-চারটে পুলিশ দু-একদিন অকুস্থলে ঘোরাঘুরি করে যায় ।
ডানদিকে ড্রাইভার শিখ সর্দারজি। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ি ও পরে জানতে পারলুম রাতকানা। বাঁ দিকে আফগান সরকারের এক কর্মচারী। পেশাওয়ার গিয়েছিলেন কাবুল বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্য । সব ভাষাই জানেন অথচ বলতে গেলে এক ফরাসি ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই জানেন না । অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর ইংরেজি না বোঝেন তবে তিনি ভাবখানা করেন যেন আপনিই যথেষ্ট ইংরেজি জানেন না, তখন তিনি ফরাসির যে ছয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন। তখনো যদি আপনি তার বক্তব্য না বোঝেন তবে তিনি উর্দু ঝাড়েন। শেষটায় এমন ভাব দেখান যে অশিক্ষিত বর্বরদের সঙ্গে কথা বলবার ঝকমারি আর তিনি কত পোহাবেন? অথচ পরে দেখলুম ভদ্রলোক অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, বিপন্নের সহায়। তারও পরে বুঝতে পারলুম ভাষা বাবদে ভদ্রলোকের এ দুর্বলতা কেন যখন শুনতে পেলুম যে তিনি অনেক ভাষায় পাণ্ডিত্যের দাবি করে বেতারে চাকরি পেয়েছেন।বাসের পেটে একপাল কাবুলি ব্যবসায়ী। পেশাওয়ার থেকে সিগারেট, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পেলেট-বাসন, ঝাড়-লণ্ঠন, ফুটবল, বিজলি-বাতির সাজ-সরঞ্জাম, কেতাব-পুঁথি, এক কথায় দুনিয়ার সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। বাদবাকি প্রায় সব কিছুই আমদানি করতে হয় হিন্দুস্থান থেকে, কিছুটা রুশ থেকে। এসব তথ্য জানবার জন্য আফগান সরকারের বাণিজ্য প্রতিবেদন পড়তে হয় না, কাবুল শহরে একটা চক্কর মারলেই হয়। সে সব পরের কথা । পেশাওয়ার থেকে জমরুদ দুর্গ সাড়ে দশ মাইল সমতল ভূমি। সেখানে একদফা পাসপোর্ট দেখাতে হলো। তারপর খাইবার গিরিসংকট।
8
দুদিকে হাজার ফুট উঁচু পাথরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে খাইবারপাস। এক জোড়া রাস্তা এঁকেবেঁকে একে অন্যের গা ঘেঁষে চলেছে কাবুলের দিকে। এক রাস্তা মোটরের জন্য, অন্য রাস্তা উট খচ্চর গাধা ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্য। সংকীর্ণতম স্থলে দুই রাস্তায় মিলে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতালের মতো টলতে টলতে এতই এঁকেবেঁকে গিয়েছে যে, যে কোনো জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে ডানে বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড় ।
দ্বিপ্রহর সূর্য সেই নরককুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে—তাই নিয়ে চতুর্দিকের পাহাড় যেন লোফালুফি খেলছে । অবাক হয়ে দেখছি সেই গরমে বুখারার পুস্তিন (ফার) ব্যবসায়ীরা দুই ইঞ্চি পুরু লোমওয়ালা চামড়ার ওভারকোট গায়ে দিয়ে খচ্চর খেদিয়ে খেদিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলেছে। সর্দারজিকে রহস্য সমাধানের অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, যাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে সত্যই এরকম পুরু জামা এই গরমে আরামদায়ক। বাইরের গরম ঢুকতে পারে না, শরীর ঠান্ডা রাখে। ঘাম তো আর এদেশে হয় না, আর হলেই বা কি? এরা তার থোড়াই পরোয়া করে । এটুকু বলতে বলতেই দেখলুম গরমের হল্কা মুখে ঢুকে সর্দারজির গলা শুকিয়ে দিল । গল্প জমাবার চেষ্টা বৃথা
কত দেশের কত রকমের লোক পণ্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কত ঢঙের টুপি, কত রঙের পাগড়ি, কত যুগের অস্ত্র-গাদাবন্দুক থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম জর্মন মাউজার। দামেস্কের বিখ্যাত সুদর্শন তরবারি, সুপারি কাটার জাঁতির মতো ‘জামধর' মোগল ছবিতে দেখেছিলুম, বাস্তবে দেখলুম হুবহু সেই রকম গোলাপি সিল্কের কোমরবন্ধে গোঁজা । কারো হাতে কানজোখা পেতলে বাঁধানো লাঠি, কারো হাতে লম্বা ঝকঝকে বর্শা । উঠের পিঠে পশমে রেশমে বোনা কত রঙের কার্পেট, কত আকারের সামোভার। বস্তা বস্তা পেস্তা বাদাম আখরোট কিসমিস আলুবুখারা চলেছে হিন্দুস্থানের বিরিয়ানি পোলাওয়ের জৌলুস বাড়াবার জন্য। আরও চলেছে, শুনতে পেলুম, কোমরবন্ধের নিচে, ইজেরের ভাঁজে, পুস্তিনের লাইনিংয়ের ভিতরে আফিং আর হাসিস না ককেনই, না আরও কিছু । সবাই চলেছে অতি ধীরে অতি মন্থরে।
পাঠান দু-বার বলেছিলেন, আমি তৃতীয়বার সেই প্রবাদ শপথরূপে গ্রহণ করলুম। ‘হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা। কে বলে বিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনা ঘটে না? আমার সকল সমস্যা সমাধান করেই যেন ধড়াম করে শব্দ হলো। কাবুলি তড়িৎ গতিতে চোখের ফেটা খুলে আমার দিকে বিবর্ণ মুখে তাকাল, আমি সর্দারজির দিকে তাকালুম। তিনি দেখি অতি শান্তভাবে গাড়িখানা এক পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। বললেন, টায়ার ফেঁসেছে। প্রতিবারেই হয়। এই গরমে না হওয়াই বিচিত্র।'
প্রয়োজন ছিল না, তবু সর্দারজি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, খাইবার পাসের রাস্তা দুটো সরকারের বটে, কিন্তু দুদিকের জমি পাঠানের। সেখানে নেমেছ কি মরেছ। আড়ালে-আবডালে পাঠান সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে। নামলেই কড়াক- পিঙ্ । তারপর কী কায়দায় সব কিছু হরণ করে তার বর্ণনা দেবার আর প্রয়োজন নেই ।
পাঠান যাতে ঠিক রাস্তার বুকের ওপর রাহাজানি না করে তার জন্য খাইবার পাসের দুদিকে যেখানে বসতি আছে সেখানকার পাঠানদের ইংরেজ দু-টাকা করে বছরে খাজনা দেয়। পরে আরেকটি শর্ত অতি কষ্টে আদায় করেছে। আফ্রিদি আফ্রিদিতে ঝগড়া বাধলে রাস্তার এপারে ওপারে যেন বন্দুক না মারা হয় । মোটর আবার চলল । কাবুলির গলা ভেঙে গিয়েছে। তবু বিড়বিড় করে যা বলছিলেন, তার নির্যাস-
কিচ্ছু ভয় নেই সায়েব- কালই কাবুল পৌঁছে যাচ্ছি। সেখানে পৌঁছে কব্ করে কাবুল নদীতে ডুব দেব। বরফগলা হিমজল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, দিল জান কলিজা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি বললুম, “আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।”
হঠাৎ দেখি সামনে একি! মরীচিকা? সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে গেট কেন? মোটর থামল। পাসপোর্ট দেখাতে হলো । গেট খুলে গেল। আফগানিস্তানে ঢুকলুম। বড়ো বড়ো হরফে সাইনবোর্ডে লেখা—
কাবুলি বললেন, “দুনিয়ার সব পরীক্ষা পাস করার চেয়ে বড় পরীক্ষা খাইবারপাস পাস করা। আলহামদুলিল্লা
(খুদাকে ধন্যবাদ)।” আমি বললুম, “আমেন ।
৫
খাইবার পাস তো দুঃখে-সুখে পেরোলুম এবং মনে মনে আশা করলুম এইবার গরম কমবে। কমলো বটে, কিন্তু পাসের ভিতর পিচ-ঢালা রাস্তা ছিল—তা সে সংকীর্ণ হোক আর বিস্তীর্ণই হোক। এখন আর রাস্তা বলে কোনো বালাই নেই। হাজারো বৎসরের লোক-চলাচলের ফলে পাথর এবং অতি সামান্য মাটির ওপর যে দাগ পড়েছে তারই উপর দিয়ে মোটর চলল। এ দাগের ওপর দিয়ে পণ্যবাহিনীর যেতে আসতে কোনো অসুবিধা হয় না । কিন্তু মোটর-আরোহীর পক্ষে যে কতদূর পীড়াদায়ক হতে পারে তার খানিকটা তুলনা হয় বীরভূম-বাঁকুড়ায় ডাঙ্গা ও খোয়াইয়ে রাত্রিকালে গোরুর গাড়ি চড়ার সঙ্গে— যদি সে গাড়ি কুড়ি মাইল বেগে চলে, ভিতরে খড়ের পুরু তোশক না থাকে এবং ছোটবড় নুড়ি দিয়ে ডাঙ্গা-খোয়াই ছেয়ে ফেলা হয় ।
লান্ডিকোটাল থেকে দক্কা দশ মাইল ।
সেই মরুপ্রান্তরে দক্কাদুর্গ অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হলো । মাটি আর খড় মিশিয়ে পিটে পিটে উঁচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে আশপাশের রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে- ফ্যাকাশে, ময়লা, ঘিনঘিনে হলদে রং। দেয়ালের ওপরের দিকে এক সারি গর্ত; দুর্গের লোক তারই ভিতরে দিয়ে বন্দুকের নল গলিয়ে নিরাপদে বাইরের শত্রুকে গুলি করতে পারে। দূর থেকে সেই কালো কালো গর্ত দেখে মনে হয় যেন অন্ধের উপড়ে নেওয়া চোখের শূন্য কোটর ।
কিন্তু দুর্গের সামনে এসে বাঁ দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। ছলছল করে কাবুল নদী বাঁক নিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছেন- ডান দিকে এক ফালি সবুজ আঁচল লুটিয়ে পড়েছে।
কাবুলি বললেন,
“চলুন দুর্গের ভিতরে যাই। পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমরা সরকারি কর্মচারী। তাড়াতাড়ি
ছেড়ে দেবে। তাহলে সন্ধ্যার আগেই জালালাবাদ পৌঁছতে পারব । ” দুর্গের অফিসার আমাকে বিদেশি দেখে প্রচুর খাতির-যত্ন করলেন। দক্কার মতো জায়গায় বরফের কল থাকার কথা নয়, কিন্তু যে শরবত খেলুম তার জন্য ঠাণ্ডা জল কুঁজোতে কী করে তৈরি করা সম্ভব হলো বুঝতে পারলুম না ।
৬
আফগানিস্তানের অফিসার যদি কবি হতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে পির হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তিন-তিনবার চাকা ফাটালো, আর ইঞ্জিন সর্দারজির ওপর গোসা করে দুবার গুম হলেন। চাকা সারাল হ্যাজি ম্যানন – তদারক করলেন সর্দারজি।
জালালাবাদ পৌঁছবার কয়েক মাইল আগে সর্দারজির কোমরবন্ধ অথবা নীবিবন্ধ কিংবা বেল্ট- যাই বলুন, ছিঁড়ে দুটুকরো হলো। তখন খবর পেলুম সর্দারজিও রাতকানা। রেডিওর কর্মচারী আমার কানটাকে মাইক্রোফোন ভেবে ফিস ফিস করে প্রচার করে দিলেন, “অদ্যকার মতো আমাদের অনুষ্ঠান এইখানেই সমাপ্ত হলো। কাল সকাল সাতটায় আমরা আবার উপস্থিত হব।”
আধ মাইলটাক দূরে আফগান সরাই । বেতারের সায়েব ও আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললুম। বাদবাকি আর সকলে হৈ-হল্লা করে করে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল । সর্দারজি তন্বী করে বললেন, “একটু পা চালিয়ে । সন্ধ্যা হয়ে গেলে সরাইয়ের দরজা বন্ধ করে দেবে।”
সরাই তো নয়, ভীষণ দুশমনের মতো দাঁড়িয়ে এক চৌকো দুর্গ। “কর্মঅন্তে নিভৃত পান্থশালাতে” বলতে আমাদের
চোখে যে স্নিগ্ধতার ছবি ফুটে উঠে এর সঙ্গে তার কোনো সংশ্রব নেই । ত্রিশ ফুট উঁচু হলদে মাটির নিরেট চারখানা দেয়াল, সামনের খানাতে এক বিরাট দরজা- তার ভেতর দিয়ে উট, বাস, ডবল-ডেকার পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভেতরে যাবার সময় মনে হয়, এই শেষ ঢোকা, এ দানবের পেট থেকে আর বেরোতে হবে না । ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। কত শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দুর্গন্ধ আমাকে ধাক্কা মেরেছিল বলতে পারি নে, কিন্তু মনে হলো আমি যেন সে ধাক্কায় তিন গজ পিছিয়ে গেলুম। ব্যাপারটা কী বুঝতে অবশ্য বেশি সময় লাগল না। এলাকাটা মৌসুমি হাওয়ার বাইরে, তাই এখানে কখনো বৃষ্টি হয় না- যথেষ্ট উঁচু নয় বলে বরফও পড়ে না । আশেপাশে নদী বা ঝরনা নেই বলে ধোয়ামোছার জন্য জলের বাজে খরচার কথাও ওঠে না। অতএব সিকন্দরশাহি বাজিরাজ থেকে আরম্ভ করে পরশুদিনের আস্ত ভেড়ার পাল যে সব ‘অবদান' রেখে গিয়েছে, তার স্থূলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তরীভূত হয়ে আছে যে, ভয় হয় ধাক্কা দিয়ে না সরালে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সূচিভেদ্য অন্ধকার দেখেছি, এই প্রথম সূচিভেদ্য দুর্গন্ধ শুকলুম।
৭
ভোরবেলা ঘুম ভাঙল আজান শুনে । নামাজ পড়ালেন বুখারার এক পুস্তিন সদাগর। উৎকৃষ্ট আরবি উচ্চারণ শুনে বিস্ময় মানলুম যে তুর্কিস্তানে এত ভালো উচ্চারণ টিকে রইল কী করে। বেতারওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, “আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন না।” আমি বললুম, “কিছু যদি মনে করেন?” আমার এই সংকোচে তিনি এত আশ্চর্য হলেন যে বুঝতে পারলুম, খাস প্রাচ্য দেশে অচেনা-অজানা লোককে যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধা নেই। পরে জানলুম, যার সম্বন্ধে কৌতূহল দেখানো হয় সে তাতে বরঞ্চ খুশিই হয়। মোটরে বসে তারই খেই তুলে নিয়ে আগের রাতের অভিজ্ঞতার জমাখরচা নিতে লাগলুম।
চোখ বন্ধ অবস্থায়ই ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রথম পরশ পেলুম; খুলে দেখি সামনে সবুজ উপত্যকা- রাস্তার দুদিকে ফসল ক্ষেত। সর্দারজি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, “জালালাবাদ” । তখন দুদিকেই সবুজ, আর লোকজনের ঘরবাড়ি। সামান্য একটি নদী ক্ষুদ্রতম সুযোগ পেলে যে কী মোহন সবুজের লীলাখেলা দেখাতে পারে জালালাবাদে তার অতি মধুর তসবির। এমনকি যে দু-চারটে পাঠান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের চেহারাও যেন সীমান্তের পাঠানের চেয়ে মোলায়েম বলে মনে হলো। লক্ষ করলুম, যে পাঠান শহরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের বেপর্দামি নিন্দা করে তারই বউ-ঝি ক্ষেতে কাজ করছে অন্য দেশের মেয়েদেরই মতো। মুখ তুলে বাসের দিকে তাকাতেও তাদের আপত্তি নেই । বেতার কর্তাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, “আমার যতদূর জানা, কোনো দেশের গরিব মেয়েই পর্দা মানে না, অন্তত আপন গাঁয়ে মানে না । শহরে গিয়ে মধ্যবিত্তের অনুকরণে কখনো পর্দা মেনে ‘ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করে' কখনো কাজ-কর্মের অসুবিধা হয় বলে গাঁয়ের রেওয়াজই বজায় রাখে।” আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “আরবের বেদুইন মেয়েরা” ।
তিনি বললেন, ‘আমি ইরাকে তাদের বিনা পর্দায় ছাগল চরাতে দেখেছি।'
গাড়ি সদর রাস্তা ছেড়ে জালালাবাদ শহরে ঢুকল। কাবুলিরা সব বাসের পেট থেকে বেরিয়ে এক মিনিটের ভেতর অন্তর্ধান । কেউ একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না, বাস ফের ছাড়বে কখন । আমার তো এই প্রথম যাত্রা, তাই সর্দারজিকে শুধালাম “বাস আবার ছাড়বে কখন?” সর্দারজি বললেন, আবার যখন সবাই জড়ো হবে। জিজ্ঞেস করলুম সে কবে? সর্দারজি যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, “আমি তার কী জানি? সবাই খেয়েদেয়ে ফিরে আসবে যখন তখন।”
বেতারকর্তা বললেন, “ঠায় দাঁড়িয়ে করছেন কী? আসুন আমার সঙ্গে।” আমি শুধালাম, “আর সব গেল কোথায়? ফিরবেই বা কখন?”
তিনি বললেন, “ওদের জন্য আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন, আপনি তো ওদের মালজানের জিম্মাদার নন । ” আমি বললুম, “তা তো নই-ই। কিন্তু যেরকম ভাবে হুট করে সবাই নিরুদ্দেশ হলো তাতে তো মনে হলো না যে ওরা শিগগির ফিরবে। আজ সন্ধ্যায় তা হলে কাবুল পৌঁছব কী করে?”
বেতারকর্তা বললেন, ‘সে আশা শিকেয় তুলে রাখুন। এদের তো কাবুল পৌঁছবার কোনো তাড়া নেই । বাস যখন ছিল না, তখন ওরা কাবুল পৌঁছত পনেরো দিনে, এখন চার দিন লাগলেও তাদের আপত্তি নেই । জালালাবাদে পৌঁছেছে এখানে সক্কলেরই কাকা-মামা-শালা, কেউ-না-কেউ আছে, তাদের তত্ত্বতালাশ করবে, খাবে-দাবে, তারপর ফিরে আসবে।'
৮
মোটর ছাড়ল অনেক বেলায়। কাজেই বেলাবেলি কাবুল পৌঁছবার আর কোনো ভরসাই রইল না। পেশাওয়ার থেকে জালালাবাদ একশ মাইল, জালালাবাদ থেকে কাবুল আরও একশ মাইল । শাস্ত্রে লেখে, সকলে পেশওয়ার ছেড়ে সন্ধ্যায় জালালাবাদ পৌঁছবে। পরদিন ভোরবেলা জালালাবাদ ছেড়ে সন্ধ্যায় কাবুল। তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, শাস্ত্র মানে অল্প লোকেই। পরে জানলুম একমাত্র মেল বাস ছাড়া আর কেউ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বেগে চলে না । সন্ধ্যা কাটল নালার পারে, নারগিস বনের এক পাশে, চিনার মর্মরের মাঝখানে। সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু চিনার-পল্লব থেকে মুছে যাওয়ার পরে ডাক-বাংলোর খানসামা আহার দিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে সেখানেই চারপাই আনিয়ে শুয়ে পড়লুম ।
শেষরাত্রে ঘুম ভাঙল অপূর্ব মাধুরীর মাঝখানে। হঠাৎ শুনি নিতান্ত কানের পাশে জলের কুলুকুলু শব্দ আর আমার সর্বদেহ জড়িয়ে নাকমুখ ছাপিয়ে কোন অজানা সৌরভ সুন্দরীর মধুর নিঃশ্বাস ।
শেষরাত্রে নৌকা যখন বিল ছেড়ে নদীতে নামে তখন যেমন নদীর কুলুকুলু শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, জানলার পাশে শিউলি গাছ থাকলে শরতের অতি ভোরে যে রকম তন্দ্রা টুটে যায়, এখানে তাই হলো কিন্তু দুয়ে মিলে গিয়ে । এ সংগীত বহুবার শুনেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এহেন সৌরভসোহাগ জীবনে আর কখনো পাইনি।
সেই আধা-আলো-অন্ধকারে চেয়ে দেখি দিনের বেলার শুকনো নালা জলে ভরে গিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে নারগিসের পা ধুয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। বুঝলুম নালার উজানে দিনের বেলায় বাঁধ দিয়ে জল বন্ধ করা হয়েছিল— ভোরের আজানের সময় নিমলার বাগানের পালা; বাঁধ খুলে দিতেই নালা ছাপিয়ে জল ছুটেছে— তারই পরশে নারগিস নয়ন মেলে তাকিয়েছে। এর গান ওর সৌরভে মিশে গিয়েছে।
আর যে-চিনারের পদপ্রান্তে উভয়ের সংগীতে সৌরভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, সে তার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাতসূর্যের প্রথম রশ্মির নবীন অভিষেকের জন্য। দেখতে-না-দেখতে চিনার সোনার মুকুট পরে নিল - পদপ্রান্তে পুষ্পবনের গন্ধধূপে বৈতালিক মুখরিত হয়ে উঠল।
এদিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হলো কার ? ভোরের নামাজ শেষ হতেই সর্দারজি ভেঁপু বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভাবগতিক দেখে মনে হলো তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন, আজ সন্ধ্যায় যে করেই হোক কাবুল পৌঁছবেন।
সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর পিতার কর্মস্থল আসামের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বৃহত্তর সিলেট জেলায়। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ সিকান্দার আলী। মুজতবা আলীর শিক্ষাজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে শান্তিনিকেতনে। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।
আফগানিস্তানের কাবুলে কৃষিবিজ্ঞান কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন তিনি । এছাড়াও দেশে-বিদেশে বহুস্থানে তিনি কর্মসূত্রে গমন করেছেন। আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মানসহ বিভিন্ন ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁর ছিল বিশেষ পাণ্ডিত্য। সাহিত্যিক রসবোধ সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনার মুখ্য প্রবণতা । তাঁর রচনায় বিচিত্র জীবনপ্রবাহের নানা অনুষঙ্গ কৌতুক ও ব্যঙ্গে রসাবৃত হয়ে উপস্থাপিত হয়। সৈয়দ মুজতবা আলীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : 'দেশে বিদেশে', ‘পঞ্চতন্ত্র’,
‘চাচাকাহিনি’, ‘শবনম', ‘কত না অশ্রুজল' প্রভৃতি। সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন
হাওড়া স্টেশন - পশ্চিমবঙ্গের একটি রেলস্টেশন। আয়তনের দিক থেকে এটি ভারতের একটি বৃহত্তর রেলস্টেশন । বর্তমানে এই স্টেশনে ২৬টি প্লাটফর্ম আছে।
প্ৰাগদেশ - কোনো কিছুর শুরুতে । পূর্বদেশ। পূর্বস্থান।
ফিরিঙ্গি - ফার্সি থেকে আগত শব্দ । এর অর্থ হলো ফরাসি বা ইউরোপিয়ান। তবে ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে সাদা চামড়ার বিদেশি মাত্রেই ফিরিঙ্গি বলে অভিহিত হতেন ।
নেটিভ - ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের নেটিভ বলে অভিহিত করতেন। এর মানে হলো স্বদেশি। যে ব্যক্তি যে-দেশে বা যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ওই দেশের বা পরিবেশের নেটিভ।
ফিয়াসে - ভালোবাসার নারী । প্রাচীন ফরাসি ভাষায় এর অর্থ প্রতিজ্ঞা ।
আলাকার্ত - Ala carte। ফরাসি শব্দ। এর অর্থ খাদ্যতালিকা অনুযায়ী ।
জাকারিয়া স্ট্রিট - কলকাতার একটি স্থান। হোটেলের জন্য বিখ্যাত। সব ধরনের খাবার পাওয়া যায়।
গৌরচন্দ্রিকা - ভূমিকা । প্রাক্কথন ।
কালোয়াত - ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি। সংগীতে পারদর্শী শিল্পী। উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো দ্রুত লয়ে ।
পেশোয়ার স্টেশন - পাকিস্তানের পেশোয়ারে অবস্থিত রেলস্টেশন ।
দিল্লি - ভারতের রাজধানী শহর । পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল শহর হিসেবে পরিচিত । আয়তনের দিক থেকে ভারতের সবচেয়ে বড় শহর এবং ভারতের প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম ।
জলন্ধর - ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অতি প্রাচীন শহর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে পরিচিত।
রাওয়ালপিন্ডি - পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে নয় মাইল দূরের শহর রাওয়ালপিন্ডি পাকিস্তানের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর।
পেশোয়ার - পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন প্রদেশের সবচেয়ে বড় শহর পেশোয়ার । খাইবার পাস-এর শেষ পূর্ব প্রান্তের হ্রদের পাশে শহরটি অবস্থিত। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে শহরটি সমৃদ্ধ।
টাঙা - টাট্টু ঘোড়ায় টানা দুই চাকার গাড়ি ।
খাইবার পাস - গিরিপথ। এই গিরিপথের মাধ্যমে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংযোগ সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম রাস্তার মধ্যে এটি অন্যতম। আলেকজান্ডার দি গ্রেট ও চেঙ্গিস খান থেকে শুরু করে মুসলিম শাসকগণ তাদের বিশ্ব বিজয়ে খাইবার পাস ব্যবহার করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধকৌশলের অংশ হিসেবে ব্রিটিশরা এই খাইবার পাস দিয়ে একটি ভারি রেলওয়ে নির্মাণ করে। বর্তমানে এই পথ দিয়ে আমেরিকা তাদের সৈন্যদের জন্য আফগানিস্তানে রসদ নিয়ে যায় ৷
বুখারা - উজবেকিস্তানের পঞ্চম বৃহৎ শহর । প্রাচীন এই শহর ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতিচর্চা ও ধর্মচর্চার জন্য বিখ্যাত। একদিকে প্রচুর স্থাপত্যকর্ম এবং অন্যদিকে মসজিদ-মাদ্রাসা এই শহরটিকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে।
জর্মন মাউজার - জার্মানের একটি অস্ত্র তৈরির কারখানার নাম মাউজার ( Mauser)। পল মাউজার এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৪ সালের ২৩এ মে কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনো এই প্রতিষ্ঠানের ডিজাইনকৃত রাইফেল ও পিস্তল সারা পৃথিবীতে বিক্রি হয়।
সামোভার - গরম পানির পাত্রবিশেষ ।
দামেস্ক - সিরিয়ার রাজধানী। সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র। চার হাজার বছর আগে শহরটি নির্মিত হয়।
কানজোখা - কাঁধ পরিমাণ ।
আফ্রিদি - পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সাহসী উপজাতি বিশেষ। পশ্চিম পেশোয়ারের প্রায় এক হাজার বর্গমাইলব্যাপী এদের বাস।
লান্ডিকোটাল - পাকিস্তানের উপজাতি শাসিত অঞ্চলের একটি শহর। খাইবার পাস-এর পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই শহর অবস্থিত।
পুস্তিন - চামড়ার জামা বা কোট
জালালাবাদ - আফগানিস্তানের একটি শহর। আদিনাপুর নামে খ্যাত। কাবুল নদী, কুনার নদী ও লাগমান দ্বীপের সংযোগস্থলে শহরটি অবস্থিত। পাকিস্তানের নিকটবর্তী আফগানিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পনগরী জালালাবাদ ।
সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত “গন্তব্য কাবুল” শীর্ষক ভ্রমণকাহিনিটি তাঁর ‘দেশে বিদেশে' (১৯৪৮) গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই রচনাটির মধ্য দিয়ে আমরা সৈয়দ মুজতবা আলীর অসাধারণ ভ্রমণ-সাহিত্যের সঙ্গেই শুধু পরিচিত হই না, অধিকন্তু তাঁর জীবনবোধ, সাহিত্যরুচি ও নিজস্ব শিল্প-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও পরিচিত হতে পারি । সৈয়দ মুজতবা আলী বিচিত্র এক জীবন যাপন করেছেন। কত জনপদ, কত মানুষ আর কত ঘটনার সঙ্গে যে তিনি এক জীবনে পরিচিত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর সেই জনপদ, সেই মানুষ আর সেই সব ঘটনাকেও তিনি দেখেছেন কখনো রসিকের চোখে, কখনো ভাবুকের চোখে এবং কখনোবা বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের মনন ও নিষ্ঠার চোখে। ফলে অনিবার্যভাবেই তাঁর সব সৃষ্টির মতো ভ্রমণ-সাহিত্যও হয়ে উঠেছে তুখোড় এক জীবনচাঞ্চল্যে ভরপুর কথামালা। “গন্তব্য কাবুল” তার ব্যতিক্রম নয়। হাওড়া স্টেশন থেকে কাবুলের উদ্দেশে যে যাত্রাটি তিনি শুরু করেছিলেন তাতে শেষ পর্যন্ত অসাধারণ রসঘন এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের প্রতিটি পর্বে কত যে কৌতুক, কৌতূহল, হাসি-ঠাট্টা, রম্য-রসিকতা আর প্রজ্ঞা ও মনন পাঠকের জন্য অপেক্ষা করে তার কোনো তুলনা চলে না। যাত্রার শুরুতেই গাড়িতে উঠতে গেলে একজন ইংরেজ হাঁক দিয়ে বলেছিলেন “ওটা ইয়োরোপিয়ানদের জন্য”। এই একটি মাত্র উক্তির মধ্যে ব্রিটিশশাসিত দুইশ বছরের ইতিহাসের একটি মাত্রা অনুভব করা যায়। আবার সেই ফিরিঙ্গির সঙ্গেই যখন শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ যাত্রা শুরু হয় আর ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাওয়া হয় নিজেদের সঙ্গে করে আনা বিচিত্র খাবার তখন অন্য এক ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। সেই ইতিহাস মানবিকতার, সাম্যের, সৌন্দর্যের। এই বিচিত্র মানুষ-জনের সঙ্গে মিলেমিশে আছে নানা ধরনের প্রকৃতি, ভূগোল, ইতিহাস ও নানা সংস্কৃতি। এই রচনায় সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতার একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের পরিচয় তুলে ধরেছেন।
Promotion